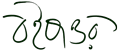
যথার্থ বিশ্বায়ন : নোয়াম চমস্কি
মুক্ত ও ন্যায্য বাণিজ্য :
উল্লেখ থাক যে আমি বিশ্বায়নের সপক্ষে। আধুনিক কালে তাদের জন্ম থেকেই বাম এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। সে জন্যই প্রতিটি ইউনিয়নকে বলা হত আন্তর্জাতিক. . . সে জন্যই আমি বার-বার লিখেছি যে গত কয়েক বছরের গ্লোবাল জাস্টিস মুভমেন্ট বা বিশ্ব ন্যায়ের আন্দোলন, পোর্তো আলেগ্রে বা মুম্বই বা অন্যত্র. . . যা বার্ষিক সম্মিলনে মিলিত হয়, তা-ই বোধ হয় সত্যিকারের আন্তর্জাতিক সংগঠনের বীজ, অর্থাৎ এমন বিশ্বায়নের, যা রক্তমাংসের জনগণ-অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়।
সত্যি, বিশ্বায়নের সবচেয়ে উৎসাহী প্রচারক তারাই, যারা ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম, বা ভিয়া কাম্পেসিনা-র মতো সম্পর্কিত সংগঠনে মিলিত হয়।
বিশ্বায়ন– অর্থাৎ অর্থনৈতিক বা অন্য কোন রকমের আন্তর্জাতিক সংহতির যে বিরোধী– এমন কাউকে আমি চিনি না। খুব আত্মনিবেদিত কোন সাধুর কথা অবশ্য আলাদা।
অর্থাৎ একটা স্তরে, শ্রমিকেরা এবং কোম্পানিগুলো একমত : প্রত্যেকে বিশ্বায়নের সমর্থক– কথাটার প্রায়োগিক অর্থে, কিন্তু তার মতাদর্শগত অর্থে নয়– যেখানে বিনিয়োগকারীর অধিকার মোতাবেক এক সংহতির কথা বলা হয়– যা তথাকথিত এক ‘মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি’র ওপর নির্মিত, যা উদারনীতিবাদ ও সংরক্ষণবাদের এক জটিল মিশ্রণ, এবং যেখানে গৃহীত নীতির ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘিত হয়।
প্রশ্নটা হল, বিশ্বায়নের রূপ নিয়ে। শব্দটাকে নিজের পছন্দমতো বানিয়ে ব্যবহারের অধিকার কারও নেই। যে-বিশ্বায়নে জনগণের অধিকার প্রাধান্য পায় না, খুব সম্ভব তা এক স্বেচ্ছাচারের রূপ নেবে, হয়তো তার চেহারা হবে অলিগার্কিক, কিংবা অলিগো-পলিস্টিক– ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার ঘনীভবনের ওপর তা নির্ভর করে, জনগণের কাছে জবাবদিহির দায়ও তার নেই।
পণ্য, পুঁজি ও জনতার স্বাধীন চলাচল :
আমি বুঝতে পারি না লোকে ভাবলেশহীন মুখে কী করে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে কথা বলে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গ্যানাইজেশন-এর নিয়ম বলে তৈরি করা সূত্রে মুক্ত বাণিজ্যের ধারণা পরিষ্কার লঙ্ঘন করা ছাড়াও সেখানে রয়েছে একচেটিয়া দাম রাখার নিশ্চয়তা, অর্থনীতির ইতিহাসে যার কোন জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।
যেমন, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য যারা গুরুতর ভাবে এক সচল সরকারি ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত রাজনৈতিক অস্তিত্বের কাছে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) এই ‘মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি’তে ঢোকার অর্থ কী?
বিষয়গুলো সূত্রায়ণের পেছনে এত গভীর প্রতারণা আছে যে মতবাদগত পুরাণের এক নিবিড় ও সূক্ষ্ম জাল না-ছাড়িয়ে এগোনোই মুশকিল।
অ্যাডাম স্মিথ-এর সঙ্গে আমি একমত যে মুক্ত বাণিজ্যের মূল অংশ হল জনগণের স্বাধীন চলাচল। আর পুঁজির স্বাধীন চলাচলের কথা যদি বলো, তো সেটা একেবারে আলাদা ব্যাপার।
রক্তমাংসের মানুষের যে-অধিকার আছে, পুঁজির তা নেই– অন্তত এনলাইটেনমেন্ট বা ধ্রুপদী উদার আদর্শে নেই। যে-মুহূর্তে আমরা পুঁজির স্বাধীন চলাচল নিয়ে কথা বলব, সে মুহূর্তে আমাদের এই ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে যে যথার্থ ও ন্যায়পরায়ণ কোন সমাজে নীতিগত ভাবে অন্তত সমস্ত মানুষের অধিকার এক, কিন্তু পুঁজির কথা বললে বাস্তবটা ভিন্ন– তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কথা বলি পুঁজির মালিকদের সম্পর্কে, ক্ষমতার হিশেবে যারা ব্যাপক ভাবে অসমান।
বাস্তব পৃথিবীতে পুঁজির স্বাধীন চলাচল মানেই গণতন্ত্রের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, তার কারণগুলো এত স্পষ্ট যে বহু কাল ধরেই আমরা তা জানি। পুঁজি এবং শ্রম নিয়ে একই স্তরে কথা বললে সেটা এত বিশ্রী ভাবে বিপথে নিয়ে যায় যে তার ভিত্তিতে কোন বিবেচক আলোচনা করা অসম্ভব।
যথার্থ বিশ্বায়ন :
যথার্থ বিশ্বায়ন কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের উৎপাদন, বণ্টন, পরস্পর-পরিবর্তন, তথ্য ইত্যাদির গণতান্ত্রিক বনাম একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করতে হবে।
এ সমস্তই সীমানা-পেরনো আন্তঃক্রিয়ার যে-কোন সুস্থ আলোচনায় আবশ্যিক–
এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সুসভ্য দুনিয়াতেও দেশের সীমানা ঘুচবে না (আমি অবশ্য তা মনে করি না, কিন্তু সে আরও এক মস্ত বিষয়)। বিশ্বায়নের যথার্থ রূপ নিয়ে প্রশ্ন করলে বহু গুরুতর প্রশ্নই উঠে আসে।
কর্মক্ষেত্রের অধিকার-সহ মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য দীর্ঘ গণসংগ্রামের সুফল যে-সমস্ত দেশে ফলেনি, সে সব দেশে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়েও কথাটা সত্যি, যদিও তা আংশিক।. . .
চিন-এর অর্থনৈতিক শক্তি খুব জটিল ব্যাপার। এক দিক থেকে, তার অনেকটাই বিদেশিদের অধিগত, আর উচ্চপ্রযুক্তির লক্ষ্য থাকায় তা ক্রমেই বাড়ছে। আর-এক দিক থেকে চিন-এর মধ্যেই ভাগাভাগি খুব তীব্র আর সেটা বাড়ছে। এ সব জটিল প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও চিন বা অন্যত্র, বা এখানকার অর্থনৈতিক বিকাশকে সামাজিক ন্যায়ের এই আন্দোলন সমর্থন করে, সেটাই তার করা উচিত– যদি অবশ্য তার মানে শ্রমিকদের ধ্বস্ত করা বা গরিব কৃষকদের পচতে দেওয়া বা পরিবেশ-পর্যাবরণের ক্ষতি করা না-বোঝায়. . .
মারিয়া আহমেদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। গ্লোবাল এজেন্ডা। জানুয়ারি ২০০৬। সন্দীপন ভট্টাচার্যের অনুবাদ। মনফকিরা প্রকাশিত ‘নতুন এই বিশ্বব্যবস্থা : কোন দিকে চলেছে দুনিয়া ২’ গ্রন্থে সংকলিত।
(এখানে প্রকাশিত লেখাপত্র শুধুই পড়ার জন্য। দয়া করে এর কোন অংশ কোথাও পুনর্মুদ্রণ করবেন না। ইচ্ছে করলে লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন, কিন্তু অনুরোধ, গোটা লেখাটি কখনওই অন্য কোন ওয়েবসাইটে বা কোন সোশ্যাল নেটওয়রকিং সাইটে শেয়ার করবেন না। ধন্যবাদ।)